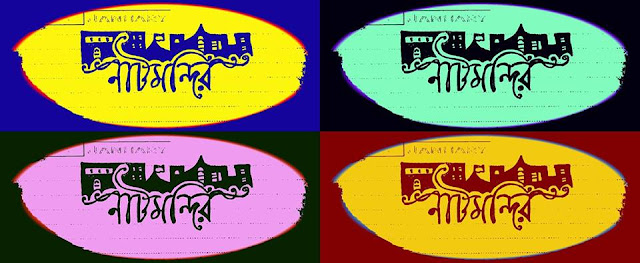“মাঝখানে কদ্দিন
হবে বলতো?” ডানহাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা আলগোছে গাড়ির জানলার কাছে ধরে আর বামহাতটা স্টিয়ারিং-এর ওপর রেখে রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই সন্দীপ জিজ্ঞেস করল।
“তা মন্দ কি?”
আমি হেসে বললাম। “নাইন্টি ফাইভে বাবা ট্রান্সফার হয়ে মেদিনীপুর শহর থেকে চলে এলেন
কাঁথি শহরে, মানে এখন যেটা কন্টাই আর কি। সঙ্গে মা আর আমি। আমি তো পুরোনো স্কুলের
পাঠ চুকিয়ে ভর্তি হলাম কন্টাই নার্সারি স্কুলে, যেখানে তোর সাথে আলাপ। তারপর
নাইন্টি সিক্সের মাঝামাঝিই তো আবার বাবার বদলির অর্ডার আসে। ততদিনে আমাদের ক্লাস
থ্রির অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ। তখনই ফিরে আসি। হিসেবমতো একুশ-বাইশ বছর তো বটেই।”
“তাহলেই বোঝ। তবে
তোর মুখের আদলটার কিন্তু বিশেষ হেরফের হয়নি। এক ওই চাপদাড়িটা ছাড়া।”
“হা হা। তা হবে। তবে
তোর মুখটা স্মৃতির প্রায় বাইরেই চলে গিয়েছিল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে যে চিনতাম না
এটা শীওর। গলার আওয়াজ তো একদমই অচেনা। তারপর হাসিটা দেখে সেই বাইশ বছর আগের
চেহারাটার হাল্কা আভাস ফিরে এল।”
“বলছিস?” একগাল
হেসে সন্দীপ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।
“আলবৎ”
বাঁয়ে জানলার
পাশে পেছনদিকে ছুটে চলা গাছপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। বাবার
ছিল বদলীর চাকরি। সেই সুবাদেই কাঁথিতে গিয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার বয়স কতই বা হবে? সাত-আট
বছর। এত ছোটো বয়সে একটা নতুন শহরে একজন বাচ্চা ছেলে যে কতটা একা হয়ে যেতে পারে,
এখন তাই ভাবি। দিন পনেরোর মধ্যেই অবশ্য স্কুলে ভর্তি হয়ে যাই ওখানে। আর সেখানেই
বন্ধুত্ব হয় সন্দীপের সাথে। তবে গাঢ় বন্ধুত্বের পাশাপাশি আর একটা জিনিস যেটা ছিল
আমাদের মধ্যে, তা হল পড়াশোনায় রেষারেষী। ও ছিল স্কুলে বরারবরের ফার্ষ্ট বয়,
হেডমাষ্টারের নয়নের মণি। স্পোর্টস আর আবৃত্তিতেও ছিল তুখোড়। ক্লাশের একটা অংশ ওকে
আড়ালে ‘পড়াকু’ বলে ডাকত, এটাও মনে আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা পড়তে পারত। ওদের বাড়ির
সামনে একটা মাঠ ছিল, যেখানে আমরা বিকেলে খেলাধূলা করতাম। সকালে আমাদের স্কুল থাকত।
দুপুর বেলাটা আমি ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেল চারটের মধ্যে চলে যেতাম ওর বাড়ির সামনে। সন্দীপকে
অবশ্য ওর মা গোটা দুপুর পড়াত। প্রায় পাঁচটা নাগাদ ওর পড়া শেষ হলে শুরু হত আমাদের
ফুটবল খেলা। মাঝখানের এক ঘন্টা আমি ভবঘুরের মতন ওদের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতাম।
সন্দীপের
টেলিফোনটা আমার কাছে এসে সোমবার, অর্থাৎ পাঁচদিন আগে। ধর্মতলায় আমার অফিসের কোনও
এক কলিগের কাছ থেকে ও আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বারটা পেয়েছিল। প্রারম্ভিক
উচ্ছ্বাস, কুশল বিনিময়, বাক্যালাপ ইত্যাদির পর প্রস্তাবটা ওই দেয়। অবশ্য এই বাইশ
বছরে আমি নিজে যে একবারও ও জায়গায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবিনি, এটা বললে মিথ্যে বলা
হবে। তবে সরকারি চাকরি, কলকাতা থেকে দুম করে বাইরে যাওয়াটা মুশকিল। খুব বেশী হলে
সপ্তাহান্তে কলেজের কোনও পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সাথে রেস্তোরাঁতে বসে ঘন্টাখানের
আড্ডা, ব্যাস। তাই তিনদিনের জন্য কাঁথিতে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবটা পেয়ে ভালোই
লেগেছিল। শুক্র, শনি আর রবি – তিনদিনের প্ল্যান। তাই অফিসে শুক্রবারের জন্য একটা
ছুটির আর্জি জানিয়ে দিলাম। শুক্রবার, মানে আজ সকালে সন্দীপ ওর সাদা হুন্ডাই
ইলান্ট্রা গাড়িটা নিয়ে চলে এসেছিল আমার বাসস্থানে। আর তার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই
বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা।
“হেডমাস্টার
সুশীলবাবুকে মনে আছে তোর?”
“তুই নামটা বলায়
মনে পড়ল।” আমি উত্তর দিলাম। “অবশ্য ওই নাম অব্দিই। চেহারা, মুখ কিচ্ছু মনে নেই। শুধু
এটুকু মনে আছে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। আমাদের কোনও একটা সাবজেক্ট পড়াতেনও যতদূর
মনে পড়ে। তোকে তো অসম্ভব স্নেহ করতেন উনি।”
“তার কারণ একটা
আছে। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছিলাম। অবশ্য...”
গাড়ির গতি কমাতে
হয়েছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই লোকালয় আছে। কারন একপাল মহিষ এসে পড়েছে গাড়ির সামনে। একটা
সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলে ‘হেট, হেট’ করতে করতে পুরো পালটাকে রাস্তা পার করিয়ে
ডানদিকে একটা মাঠের মধ্যে নেমে গেল। জন্তুগুলোর পায়ে পায়ে ধূলো উড়ে জায়গাটাকে হলুদ
আর ধোঁয়াটে করে দিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দূরের সবুজ গাছপালা, ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি,
ধানক্ষেত, কয়েকটা উঁচু-নিচু টিলা – একেবারে ছবির মত মনে হয়। গ্রামবাংলা বলে একটা
ব্যাপার যে এদেশে আছে, কলকাতায় বসে তা প্রায় মাথাতেই থাকে না। আসলে সিটি আর
কান্ট্রিলাইফের মধ্যে যে বিস্তর একটা ফারাক আছে, সেটা শুধু এই বন-জঙ্গল,
নদী-গাছপালা, বা উঁচু ইমারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, তা ছড়িয়ে পড়ে মানুষের
মনেও।
আধখোলা কাঁচের জানালা দিয়ে দূরের
গাছপালাগুলোর দিকে দৃষ্টি চলে যেতে বুঝলাম সেগুলো হাওয়ায় দুলছে। আমরা কলকাতা থেকে
দক্ষিণ-পশ্চিমে চলেছি সমুদ্রের দিকে। পূবের আকাশে রোদের তেজ খানিকটা থাকলেও ওপাশের
জানালা দিয়ে তাকিয়ে বোঝা গেল, পশ্চিমের আকাশ ছাই রঙের মেঘে ঢাকা। সময়টা জুনের
মাঝামাঝি। গত তিন চার মাস বৃষ্টি প্রায় হয়নি বললেই চলে। তাই এখন বৃষ্টি হলে পুরো
আকাশ জুড়ে জল নামবে।
“...অবশ্য তুই
স্কুলে আসার পর ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। বলতে পারিস আমি একজন পারফেক্ট
কম্পিটিটর পেয়ে গিয়েছিলাম।”
“তুই তো বরাবরের
স্টুডিয়স ছিলি, ভাই।” আমি বললাম।
“তা ছিলাম। তবে
তোর মতন মেরিটটা ছিল না। বিজ্ঞান মেধা পরীক্ষাটার কথা মনে পড়ে?”
“ওটা মনে আছে। জেলার
মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম। তবে একটা আফশোস রয়ে গিয়েছিল। প্রথম পুরস্কারের সোনার মেডেলটা
কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত পাঠাননি। এটা অনেকদিন মনে রয়ে গিয়েছিল।”
একথার সন্দীপ কোনও উত্তর দিল না। ওর নজর
গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনের দিকে। কয়েকটা বড় বড় জলের ফোঁটা কাঁচটার ওপর এসে পড়তে শুরু করেছে।
পশ্চিমে যে কালো মেঘটা দেখেছিলাম সেটা এরই মধ্যে কাছে এসে পড়ল নাকি?
কোলাঘাট হয়ে
মেচেদা অবধি এসে একটা পেট্রোল পাম্প দেখে আমরা গাড়ি থামালাম। টিপটিপ বৃষ্টিটা এখনও
পিছু ছাড়েনি। গাড়িতে তেল ভরে নিয়ে সামনেই একটা রেস্তোরাঁতে ঢোকা গেল। রুটি আর
মাংসের অর্ডার দিয়ে বসে সন্দীপ একটা সিগারেট ধরালো।
“আমার ডাউনফলের
শুরুটা ওখানেই হয় বলতে পারিস।” সন্দীপ বলল। “বছর কয়েকের মধ্যে শুনেছিলাম তুই চলে
গিয়েছিস দুন স্কুলে পড়তে। তাই যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা চলে গেলেন তখন আমার
ক্লাস টেন, ষোলো বছর বয়েস। সতেরোয় ব্যাবসায় নামি। শুরু করি লোহা-লক্কড়ের ব্যাবসা
দিয়ে। সেটা ডাহা ফেল করে। সাড়ে উনিশ বছর বয়েসে কিছু মূলধন যোগাড় করে একটা কাঠের
ব্যাবসা খুলে বসি। বরাতজোরে এটা টিকে যায়।”
“টিকে যায় কি
বলছিস! শুনলাম তো তুই এখন বিশাল বড়লোক।”
এ কথার জবাব ও দিলনা।
শুধু মুচকি হেসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আরেকটা সিগারেট ধরাল। এক
ঝলকের জন্য ব্র্যান্ডটার দিকে চোখ চলে গেল। বিলিতী কোম্পানী, বেনসন এন্ড হেজেস। বিলিতী
জিনিষের প্রতি আকর্ষণ বড়লোকদের একটা অতিপ্রাচীণ দোষ বলা যায়। অবশ্য এটা দোষ না গুণ
সেটাও বিতর্কসাপেক্ষ। সন্দীপকে আক্ষরিক অর্থেই একজন সেলফ-মেড পার্সেন বলা চলে। অল্পবয়সে নিজের বাবাকে হারানোর পর যেভাবে নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থাপন
করেছে, তাতে কিছু বাহুল্য থাকার অহংকার ওর পক্ষে স্বাভাবিক।
লাঞ্চের পর্ব শেষ করে গাড়িতে ফিরে আসছি,
এমন সময়ে বৃষ্টির জোরটা বাড়ল। গাড়ি লক করে স্টার্ট করতেই উইন্ডস্ক্রীনের ওয়াইপার
তার কাজ শুরু করে দিল। অঝোর ধারায় বৃষ্টির মধ্যে আবছা, অস্পষ্ট হয়ে পড়া দুপাশে
দূরের গাছপালা আর সড়কের ওপর ফুল স্পীডে চলা একটা গাড়ির মধ্যে দুই বন্ধু।
“ভাল কথা,” আমি
জিজ্ঞেস করলাম, “থাকার ব্যাবস্থার কথা কিছু ভেবেছিস?”
“আজকের মত আপাততঃ
একটা হোটেলে উঠতে হবে। যদিও তারপর একটা
সারপ্রাইজ থাকছে।”
“কিরকম?”
“...নাটমন্দির
মনে পড়ে?”
এবার বেশ অবাক
হলাম। নাটমন্দিরের কথাটা এতদিনে প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। বাইশ বছর আগে কাঁথিতে বদলি
হওয়ার পর বাবা আমাদের যে বাড়িটিতে ভাড়ায় থাকার জন্য নিয়ে যান, তার তদানীন্তন মালিক
ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। ভদ্রলোকের বাপ-দাদুর আমলকার জমিদারী ছিল ওখানে। বাড়িটা
ছিল প্রকান্ড, আর নামটাও ছিল জমকালো – ‘মজুমদার ভিলা’। জমিদার বংশের মানানসই।
প্রকান্ড একটা সদর, বাহির মহল একখানা, মাঝের একটা বিশাল দালান পেরিয়ে ডানদিকে ছিল
একটা নাটমন্দির। প্রাণকৃষ্ণবাবুর ঠাকুর্দার আমলে এখানে পূজাপাঠ, নৃত্যগীত এবং
কালেকস্মিনে যাত্রাপাঠ ইত্যাদি পরিবেশনা হত বলে শোনা যায়। এটা পেরিয়ে ছিল
অন্দরমহল। যদিও আমি যে সময়টায় বাড়িটায় ছিলাম, বাড়িটার শতকরা সিকি শতাংশই বাসযোগ্য
ছিল। তার একটা প্রধান কারন ছিল এই যে, পূর্বপুরুষ জমিদার হলেও স্বাধীন ভারতে জমিদারি
ফলানোর অধিকার প্রাণকৃষ্ণবাবুর ছিল না। ক্ষেতিবাড়ি করানোর লোকজন থাকলেও তা থেকে যা
আয় হত, তা অধিকাংশই বাড়ি দেখভালের পেছনে খরচ হয়ে যেত। আমাদের মতোই আরও একটি
পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল বাইরের মহলের একটি অংশে। মনে পড়ল অব্যাবহৃত
নাটমন্দিরের আনাচে কানাচে ছোটোবেলায় আমার আর সন্দীপের খেলে বেড়ানোর কথা।
“সে জিনিষ এখনও
আছে নাকি? যতদূর মনে আছে জায়গাটা তখনই ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থায় ছিল।”
“ইয়েস স্যার। সে
জায়গা আছে। যদিও বাসযোগ্য নয়, তবে একটা রাত কাটানোর মত অবস্থায় নিশ্চয়ই হবে।
সাপখোপের ভয় নেই, সঙ্গে আলাদা ব্যাবস্থা আছে।”
ঘড়ির কাঁটায় যখন ঠিক তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট, আমরা কাঁথি শহরে পৌঁছলাম। বাইশ
বছর আগের স্মৃতি হলেও এটা মনে পড়ল যে, ছোট্ট শহরটায় দুটো বাসস্ট্যান্ড ছিল। একটা
খড়গপুর, অর্থাৎ কাঁথি থেকে খড়গপুর ও মেদিনীপুরের অন্যান্য গ্রাম ও শহরের উদ্দেশ্যে
পাড়ি দেওয়া বাসের স্ট্যান্ড, আর একটা হাওড়া বাসস্ট্যান্ড – এখান থেকে হাওড়া
অভিমুখে যত বাস ছিল তা চলত। যদিও মাত্র সাত বছর বয়সে শুধু এক বছরের জন্যেই এই
শহরটায় ছিলাম, তবুও আজ প্রায় দু’ দশকেরও বেশী সময়ের পর অনেক ছোটোখাটো কথা মনে পড়ে
গেল।
আমরা প্রথমে একটা হোটেলে
উঠলাম। হাতমুখ ধুয়ে হোটেলের বারান্দায় বসে কফি আর টোস্ট খেতে খেতে সন্দীপ ওর
প্ল্যানটা জানাল।
“দেখ আকাশ, আমার
প্ল্যানটা হল এরকম। আজকের রাতটা আমরা হোটেলেই থাকছি। কাল সকালবেলা হোটেল থেকে
মালপত্র সমেত চলে যাওয়া যাবে ‘মজুমদার ভিলা’-তে। ওখানে আপাততঃ চৌকিদার গোছের একজন
লোক থাকে। তাকে বলে কয়ে একরাত্রির জন্য ওই বাড়ির কোনও একটা ঘরে থাকার বন্দোবস্ত
করতে হবে। যদিও ঘরটা শুধু ম্যানেজ করার জন্যই। আমি চাইছি রাতটা ওই নাটমন্দিরেই
কাটাব। কি বলিস?”
নাটমন্দিরে রাত
কাটানোর প্ল্যান শুনে পুরোনো দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। তখন আমাদের বয়স হবে
সাত বা আট। নাটমন্দিরের চাতাল, দোতলার ঘোরানো সিঁড়ি, ওপরে জালি দেওয়া ঘেরা অংশ – যেখানে জমিদার আমলে মহিলামহলের সদস্যরা বসে নাটমন্দিরের নাচ-গান, নাটক ইত্যাদি
দেখতেন – এইসব জায়গা ছিল আমাদের খেলাধূলা করার অবাধ এলাকা। স্কুলের ভেতরের
বন্ধুত্ব ছাড়াও স্কুলের বাইরের বেশীর ভাগ সময়েই আমরা খেলে বেড়াতাম হয় সন্দীপদের
বাড়ির সামনের মাঠে ফুটবল খেলে, নয়তো ‘মজুমদার ভিলা’-এর আনাচে কানাচে। বেশীর ভাগ ওই
নাটমন্দিরেই।
রাতটা কোনওমতে
হোটেলে কাটিয়ে দেওয়া গেল। বৃষ্টির রেশটা যে তখনও পিছু ছাড়েনি, এটাও বোঝা গেল। সারা
রাত ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা চলতেই লাগল। যদিও আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আছে
পরিষ্কার আকাশের, তবু মনটা আনচান করতে লাগল। এতদিন পর এই জায়গায় এসে শুধুমাত্র
বৃষ্টির জন্য ঘোরাঘুরি আর থাকাটা মাটি হয়ে গেলে তার থেকে খারাপ জিনিষ আর হয় না।
সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল বাইরে চড়া
রোদ। একটা ভালো দিনের শুরু। হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট করে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ‘মজুমদার
ভিলা’-এর উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটেই চলা। কাঁথি শহরটা দৈর্ঘ্যে খুব বেশী হলে চার-পাঁচ
কিলোমিটার আর প্রস্থে বড়জোর দুই-তিনেক। হোটেল থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল এক-দেড়
কিলোমিটারের মতন রাস্তা। মনে পড়ল চলার পথে এই রাস্তাতেই বাঁয়ে ঘুরে মিনিট পাঁচেক
এগিয়ে ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। ডানদিকে একটা খেলার মাঠ পেরিয়ে ছিল সন্দীপদের পুরোনো
বাড়িটা। এখানটায় আমরা খানিকক্ষণ থামলাম। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সন্দীপ একটা
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।
সময় মাঝে মাঝে মানুষকে কত একা করে দেয়,
আমি চিন্তা করলাম। শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোকে মানুষ সবসময়ে তার সুখের স্মৃতিগুলোর
সাথেই জড়িয়ে রাখে। জীবনে বেড়ে ওঠার নামই কি আসলে দুঃখ? হয়তো তাই। নাহলে দুই দশকেরও
বেশী সময়ের পর আমাদের তাগিদই বা কি থাকত একটু সুখের স্মৃতিগুলো ঝালিয়ে নেওয়ার?
সন্দীপের মুখে একটা কালো ছায়া নেমে
এসেছিল। সেটা কাটানোর জন্যই প্রশ্ন করলাম, “কাঁথি ছাড়লি কবে?”
“কাঠের ব্যাবসাটা
মোটামোটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পরই। সাপ্লাই আর ডীলারদের কাজে কলকাতায় যাতায়াত ছিলই। প্রথমে
ভাড়ায় একটা ছোটোখাটো অফিস খুলে বসি। আড়াই বছর পর কলকাতাতেই একটা ফ্ল্যাট কিনে মাকে
নিয়ে চলে আসি। ফ্ল্যাটেরই একটা ঘরকে এখন অফিসঘর বানিয়েছি।”
মনে পড়ল সন্দীপের
বর্তমান অর্থ ও প্রতিপত্তির কথা। তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।
“এতদিন পর তোর
হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কি করে বল তো?”
সন্দীপ হাসল। বলল,
“কারন একটা নিশ্চয়ই আছে। এবং সেটা যথেষ্ট পাকাপোক্ত, এটুকু বলতে পারি। তবে এখন আর
এবিষয়ে কথা নয়।”
কথা বন্ধ করতে
হল। তার কারন আমরা এসে পড়েছি ‘মজুমদার ভিলা’-এর সদর ফটকে। একসময়ে এখানে মোটা লোহার
রেলিং দেওয়া দরজায় আটকানো থাকত গেট। এখন সেসব ভেঙ্গে শুধু কাঠের উঁচু দরজাটাই যা পড়ে আছে।
চৌকিদারের সাথে
বন্দোবস্ত করতে সময় লাগল না। বৃদ্ধ লোকটি আধা বাংলা আধা বিহারী হিন্দীতে বিড়বিড় করে
“কুছ বখশিস হুজুর...” বলে উঠতেই দেখলাম সন্দীপ ওর মানিব্যাগটা থেকে পাঁচশো’ টাকার
কড়কড়ে চারটে নোট বের করে লোকটার হাতে গুঁজে দিল। চৌকিদার তিনবার সেলাম ঠুকে রাতের রান্নার
উপকরণ জোগাড় করতে চলে গেল।
চৌকিদার লোকটার কাছ থেকে নেওয়া চাবি
দিয়ে গেস্টরুমটা খুলে মালপত্রগুলো সেখানে রেখে আমরা গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখতে
বেরোলাম। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই হয়তো ভালো। বাইরের মহল আর ভেতরের মহলের মাঝখানে
প্রকান্ড একটা দালান। বড় বড় স্তম্ভগুলোর চুন-সুরকি খসে পড়ে গোটা বাড়িটার কঙ্কাল
বেরিয়ে পড়েছে। ভেতরের মহলের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন। দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে গিয়ে
বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে এখানে সেখানে। ছাদের দিকটায় চোখ যেতে দেখলাম বৃষ্টির
জলে শুধুই ঘাস, ফার্ণ আর শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে সেখানে। এখানে সেখানে পাখির বাসার
চিহ্ন, পাখির বিষ্ঠা পড়ে আছে। জায়গাটা অতীতের ধ্বংসাবশেষ বললেও কম বলা হয়। ভেতরের
দিকে একটা ছোটোমতন বাগান ছিল মনে পড়ল। জায়গাটায় এসে দেখা গেল সেই বাগান এখন এক
মানুষ উঁচু ঘাসের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। একটা জমিদার বংশ এভাবে
শেষ হয়ে গেল। চৌকিদার বলছিল এই বাড়ির শেষ উত্তরাধিকারী আসামের কোনও এক টি-এস্টেটে
কাজ করে। তারই আদেশে এবং মাসিক যৎকিঞ্চিত মাইনেতে সে রক্ষা করে চলেছে বাড়িটা। দীর্ঘশ্বাস
ছাড়লাম। হয়তো ডিসপুটেড প্রপার্টি বলে সরকারও সরিয়ে রেখেছে জায়গাটাকে।
এবার নাটমন্দিরের দিকটায় পা বাড়ালাম। এই
জায়গাটা অনেকখানি ছড়ানো। অন্দর মহলের সাথেই লাগোয়া ডানপাশে ঘেরা অনেকটা জায়গা। আগেই
বলেছি, এখানে জমিদার আমলে একসময়ে নাটক, নাচগান এসব হত। প্রতি বছর দূর্গাপূজাও হত
এখানে। পরে অবশ্য সেসব বন্ধ হয়ে যায়। চওড়া দালানের শেষপ্রান্তে দুধারে ঘোরানো
সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরদিকে একটা জালি দেওয়া অংশে। এটা ছিল মহিলাদের বসার জায়গা। সিঁড়িটা
বহুকালের অব্যাবহারের ফলে নোংরা আর শ্যাওলা পড়া। ওপর দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল ছাদের
অনেকটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে দিনের আলো সোজাসুজি এসে পড়ছে নাটমন্দিরের মেঝের
কিছুটা জায়গা জুড়ে। মেঝের একটা কোণায় একটা সাপের পুরোনো খোলস পাওয়া গেল। সর্বনাশ!
এখানে বিষধর সাপ থাকলে তো রাত কাটানো মুশকিল।
কিন্তু এর নিদান তখনই পাওয়া গেল। সন্দীপ
দেখলাম এবার এগিয়ে এসে ব্যাগ থেকে একটা কালো কাঁচের শিশি বের করে চারিদিকে একটা
তরল ছড়িয়ে দিতে লাগল। কার্বলিক অ্যাসিড। যাক, তাহলে এই ব্যাপারটা ওর মাথায় ছিল। এ
জিনিষ ছড়িয়ে রাখলে রাত্রে আর কোনও সাপ বাবাজি বিরক্ত করার জন্য এমুখো হবেন না।
“এ জিনিষ ভূতকেও
তাড়ায় নাকি?” আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।
“এ বাড়ির যা
অবস্থা, তাতে কয়েক ডজন ভূত রাত্রে আনাগোনা করলেও অবাক হব না।” সন্দীপ অর্ধেক খালি
বোতলটা আবার ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল।
কথাটা সত্যি। গাঁ-গঞ্জে এরকম আধা ভেঙ্গে
পড়া জমিদার বাড়িতে ভূতের দেখা পাওয়া যায় - একথা ছোটোবেলা থেকেই সব ভৌতিক
গল্প-উপন্যাসে পড়ে এসেছি। তা স্বচক্ষে সেরকম কোনও জিনিষ প্রত্যক্ষ করা গেলে সেটা
মন্দ ব্যাপার হবে না।
এর মধ্যেই সন্দীপ
দেখলাম ঘোরানো সিঁড়িগুলো দিয়ে ওপরে একপা একপা করে উঠতে শুরু করেছে। মতলব কি? এই
বাড়ির যা অবস্থা দেখছি, হঠাৎ করে সিঁড়িশুদ্ধ গোটা জায়গাটা ভেঙ্গে পড়লেও আশ্চর্য হব
না। কলকাতা থেকে এতদূর এসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়লে মুশকিল।
সিঁড়ির সাত-আট ধাপ উঠে সন্দীপ দেখলাম ডাইনে
দেওয়ালের লাগোয়া একটা কুলুঙ্গির মত জায়গায় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। মনে হল হাতড়ে কিছু
খুঁজছে। সর্বনাশ! পাখির ডিম-টিম খোঁজার তালে আছে নাকি?
আধ মিনিট এদিক-ওদিক
হাতড়ে শেষটায় আবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে আমার জিজ্ঞাসাপূর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে সন্দীপ
বলল, “একটা জিনিষ ছিল, বহু বছর আগে। খুব সম্ভবতঃ আমার আগে কারোর হাত পড়েছে। এখানে
আসার আসল কারনটা ভেস্তে গেল।”
সন্দীপ যে এত
রহস্য কেন করছে তা বুঝলাম না। তবে এবিষয়ে আমিও আর কোনও উচ্চবাচ্য করলাম না।
সারাটা দিন আমরা
এদিক ওদিক ঘুরে কাটালাম। প্রথমে যাওয়া গেল কন্টাই নার্সারি স্কুলে, যেখানে আমরা
একবছর একসাথে পড়াশোনা করেছিলাম। ছোটোবেলার স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হল
না। যদিও স্কুলের উঁচু দেওয়ালগুলোকে এখন আর অতটা উঁচু বলে মনে হল না। ক্লাসরুমের
টেবিল-চেয়ারগুলোকেও এখন অনেকটাই নিচু মনে হয়। বয়সের ধর্ম।
স্কুল থেকে
বেরিয়ে একবার এখানকার বাজারের দিকটায় যাওয়া গেল। নিউ মার্কেট এরিয়াটা আগের চেয়ে
অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখলাম। কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা করে দুপুরের খাওয়াটা
বাইরেই একটা হোটেলে সেরে আমরা ফিরে পড়লাম।
সময়টা বিকেল। গতকাল সারাদিন বৃষ্টি
থাকলেও আজ সারাদিনই আকাশ পরিষ্কার ছিল। দিনের আলোর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা কাজে
লাগিয়েই আমরা দুজনে মিলে নাটমন্দিরের চাতালের একটা কোণাতে রাত কাটানোর মতন একটা
ব্যাবস্থা করে নিলাম। ব্যাবস্থা বলতে চৌকিদার লোকটাকে দিয়ে কিছুটা জায়গা ধুয়ে মুছে
সাফ করিয়ে দুটো তোষক, চাদর আর বালিশ পেতে দেওয়া। চৌকিদার দেখলাম একটা হ্যাজাক
জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। “কুছ পরোয়া নহী” বলে একটা হাঁক পাড়লাম।
বৃদ্ধ লোকটা আরও কয়েকবার দোনামানা করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে
গেল সন্ধ্যে সাড়ে ন’টায় আমাদের রাতের খাবার গেস্টরুমে দেওয়া হবে। তারপর সে নাকি
আফিম খেয়ে শুয়ে পড়ে এবং গোটা রাত তার কোনও হুঁশ থাকে না। তাই খাওয়ার জল বা
অন্যান্য কিছু দরকারি জিনিষ চাওয়ার হলে আমরা যেন এখনই চেয়ে নিই।
রাতের খাওয়া দাওয়া করে যখন আমরা
ফিরে এলাম, হাতঘড়ি বলছে রাত এগারোটা। যদিও আমাদের সাথে টর্চ আছে, তবুও যেন মনে হল
একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখলেই ভালো হত। সন্ধ্যে সাড়ে ছ’টার দিকে আকাশে একবার চাঁদ
উঠেই মিলিয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। এখন চারিদিকে শুধুই অন্ধকার। অন্দরমহলের বাগানটা
থেকে অজস্র ঝিঁঝিঁর ডাক আসছে। আজ খুব সম্ভবতঃ এখানে কোথাও পুজো আছে। একটা খুব
ক্ষীণ ঢাক, ঢোল আর সংকীর্তনের আওয়াজ আসছে অনেক দূর থেকে। কিছুক্ষণ পর সেটাও বন্ধ
হয়ে গেল। একটা চামচিকে বা বাদুড়ের ডানা ঝাপটিয়ে ওপরের বাহির মহলের এক বারান্দা
থেকে আরেক বারান্দায় চলে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ।
নাটমন্দিরের
চাতালটার এক কোণায় পাশাপাশি দুটো বিছানা পাতা হয়েছে। এর মধ্যে একটায় আমি গিয়ে
বসলাম। সামনের চওড়া উঠোনের মতন জায়গাটাতে সন্দীপ পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে টর্চটা
জ্বেলে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করছে। এরই মধ্যে তামাকের একটা কটূ গন্ধ পেয়ে বুঝলাম এবার
ও একটা সিগারেট ধরিয়েছে।
সন্দীপের হাবভাব একটু অস্বাভাবিক
লাগছে। বিকেলের ওই ঘটনার পর ও কিছুটা যেন গুম মেরে গেছে। হাঁ-হুঁ করে জবাব দিচ্ছে।
‘এখানে আসার কারনটা ভেস্তে গেল’ বলতে ও ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিল?
চক বাঁধানো
চাতালের একটা কোণায় ফ্যাকাশে হলুদ রঙের একফালি আলো এসে পড়তে এবার বুঝলাম মেঘ সরে
গিয়ে চাঁদ উঁকি মারছে আকাশে। পুরো চাতালটা, ওপরের বারান্দা আর সন্দীপের চেহারাটা –
এ সবই অন্ধকারেও খানিকটা স্পষ্ট লাগছে। আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে হেঁটে কয়েক পা
এগিয়ে উঠোনটায় নেমে দাঁড়ালাম।
“তোর কি হয়েছে বল
তো?” আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম।
কয়েক মুহুর্ত চুপ
করে থেকে সন্দীপ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, “সব কথা কি আর অত সহজে বলা যায় রে? শুধু
একটা কথা বলতে পারি, হেডমাস্টার সুশীলবাবুর মুখ আমি রাখতে পারিনি। উনি আমাকে
স্কুলের সেরা ছাত্র বলে এসেছিলেন স্কুলের শেষদিন পর্যন্ত। তার মর্যাদা আমি রাখতে
পারিনি।”
এই কথায় রহস্য কমার বদলে আরো বেড়ে গেল। সন্দীপের
স্কুলের সেরা ছাত্র হওয়া বা না হওয়ার সাথে বাইশ বছর পর ‘মজুমদার ভিলা’-তে ফিরে
আসার সম্পর্ক কি? মর্যাদা রাখার ব্যাপারটা...
আমার চিন্তার সূত্রটা মাঝপথেই থেমে
গেছে। সন্দীপও দেখলাম বিছানাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছে।
একটা শব্দ।
শব্দটা কোথা থেকে
আসছে তা জানার উপায় নেই। একটা হালকা, ধুপ ধুপ আওয়াজ। খুব চেনা চেনা লাগছে। অথচ এত
ক্ষীণ যে ধরা যাচ্ছে না। কয়েকবার হয়েই শব্দটা থেমে গেল।
আমাদের হাতের টর্চগুলো জ্বালিয়ে এদিক
ওদিক ফেলেও কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই আওয়াজটা আবার
শুরু হল। এবার আওয়াজ স্পষ্ট। এবং শব্দটা আগেরবার চেনা লাগার কারনটাও পরিষ্কার হয়ে
গেল। টর্চের আলো এদিক ওদিক ফেলার মাঝেই সন্দীপের সাথে আমার একবার চোখাচোখি হয়েছে।
এবং আমাদের দুজনের মুখ দিয়ে একই সময়ে একটা কথা অস্ফুটে বেরিয়ে পড়েছে।
“ফুটবল!”
একবিংশ শতকের
কলকাতা শহর থেকে দেড়শো’ কিলোমিটার দূরে এক ছোট্ট শহরের অতি প্রাচীন এক জমিদার
বাড়িতে মাঝরাতে কে বা কারা ফুটবল নিয়ে খেলছে।
শব্দটা কোথা থেকে আসছে বলা দুষ্কর। হতে
পারে এই বাড়ির লাগোয়া মাঠে রাত্রে খেলা হচ্ছে এবং তারই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে
কানে। কিন্তু সেই ধারণা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। মাঝরাতে এই অন্ধকার আধা শহরের এক
কোণে কোনও পুরোনো জমিদার বাড়ি সংলগ্ন মাঠে কেউ ফুটবল খেলবে, এটা ভেবেও হাসি পায়।
শব্দটা ইতিমধ্যে
আবার থেমে গেছে। চৌকিদারকে ডাকলে যে কোনও ফল হবে না সেটা জানি। সে আফিমের নেশায়
চুর হয়ে ঘুমোচ্ছে। হ্যাজাকটা কেন চেয়ে নিলাম না সেটা ভেবে আবার আফশোষ হল। অন্ততঃ
যদি অতর্কিতে চোর হানা দেয় তাকে রুখতে পারা যেত। অবশ্য আমাদের সাথে মূল্যবান এমন
কোনও জিনিষ নেই যার খোঁজে চোর চুরি করতে আসবে। তবে একথা কি আর চোর জানে? সশস্ত্র
চোরকে আর যাই হোক, টর্চের আঘাতে বাগে আনা যাবে না।
আমরা দুজনে আবার
নাটমন্দিরের চাতালে আমাদের তোষকের বিছানায় ফিরে এসেছি। সন্দীপ দেখলাম প্যান্টের
পকেট হাতড়ে লাইটার বের করে আরেকটা সিগারেট ধরালো। আগুনের হালকা আলোয় বুঝলাম ওর
কপালে চিন্তা আর দ্বিধার হাল্কা ছাপ।
“তোকে এতগুলো বছর
একটা কথা আমি বলিনি রে, আকাশ। বলিনি, কারন সেটা আমি বলতে পারিনি। একটা কথা যেটা
বলা যায় না।”
আমি চুপ। আমার
মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে। কিন্তু সেটা এতটাই অসম্ভব, যে আমি নিজের মনকেও
বিশ্বাস করতে পারছি না।
ও বলে চলল,
“আজকের বিকেলে আমার ওই খোঁজাখুঁজি যদি বিফলে না যেত, তাহলে এতদিনের পুরোনো সব
গ্লানি আমার মন থেকে মুছে যেত। কিন্তু আমি পারলাম না ভাই। আমি পারলাম না।”
ওর শেষ কথাগুলো কিরকম
হাহাকারের মতন শোনালো। এটুকু বুঝেছিলাম যে কলকাতা থেকে আমাকে নিয়ে এত বছর পর কাঁথি
আসার মধ্যে সন্দীপের একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমার মনে তখন থেকেই একটা সন্দেহ ক্রমাগত
ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু যে জিনিষ বিফলে চলে গেছে তাকে আর খুঁচিয়ে লাভ নেই ভেবে কিছু
বললাম না।
হাতঘড়িতে সময়
দেখাচ্ছে রাত দেড়টা। আজ সকালে দেরী করে ঘুম ভেঙ্গেছিল বলেই কিনা কে জানে, ঘুম খুব
একটা পাচ্ছে না। জলের বোতলটা বের করে খানিকটা জল খেয়ে একবার নিচের উঠোনটায় পা
বাড়িয়েছি, এমন সময়ে আরেকটা শব্দ পাওয়া গেল।
এ শব্দ সম্পূর্ণ
আলাদা। এই আওয়াজ পায়ের আওয়াজ। মানুষের পায়ের। এবং সেটা আসছে নাটমন্দিরের ছাদের অংশ
থেকেই। পায়ের মালিক যে একের বেশি সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা যেখানে বসে
আছি, পায়ের আওয়াজ আসছে তার ঠিক ওপরে ছাদের অংশ থেকে। সামনে আরও এগিয়ে পড়বে সিঁড়ি। সিঁড়ির
ঠিক ওপরেই ছাদের অনেকটা অংশ ভাঙ্গা, যেখান থেকে অনেকটা চাঁদের আলো এসে নাটমন্দিরের
চাতালটাকে আলোকিত করে রেখেছে।
সন্দীপের দিকে
তাকিয়ে বুঝলাম আমার মত ও সচকিত হয়ে উঠেছে। ছাদ থেকে নিচে নামার একমাত্র উপায় ওই
সিঁড়ি। দুজনে টর্চদুটোকে হাতিয়ারের মত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।
আচমকা একটা কান্ড ঘটল। সিঁড়ির ওপরে
ছাদের যে অংশটা ভাঙ্গা ছিল, সেখান থেকে একটা প্রমাণ সাইজের ফুটবল সোজা নিচে পড়ে
কয়েকটা ড্রপ খেয়ে নিচের চাতালটায় পড়ে গেল।
আর তার ঠিক পরেই
যেটা ঘটল তাতে আমার দেহের সমস্ত রোম একসাথে খাড়া হয়ে উঠল।
সিঁড়ির ওপরের
জায়গাটা থেকে এক পা এক পা করে নেমে আসছে অস্পষ্ট অবয়বের একটা সাত-আট বছরের বাচ্চা
ছেলে। ঠিক বারোটা ধাপ নেমে সে নিচে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে চাঁদের আলো চাতালটায়
সরাসরি এসে পড়েছে।
“কে?”
সন্দীপের মুখ
দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে। তার কারন আর কিছুই না,
আমাদের থেকে হাত বিশেক দূরে যে বাচ্চাটি এসে দাঁড়িয়েছে, সে।
চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এসে পড়েছে
বাচ্চাটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটায়। আর তার মুখ এখন স্পষ্ট।
এ মুখ আমার চেনা।
বাইশ বছর পরের সন্দীপকে দেখে চিনতে কষ্ট হলেও এই চেহারা আর মুখ আমার ভুলবার নয়। সেই
গোল গোল বিস্মিত চোখ, এলো চুল আর হঠাৎ অপরচিত লোককে দেখে ঈষৎ হাঁ করা মুখ। কোনও এক
অদ্ভুত মায়াবলে আমাদের সামনে বিশ হাত তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে বাইশ বছর আগের সন্দীপ।
এবং তার দৃষ্টি এখনের সন্দীপের দিকেই।
কয়েকটা মুহুর্ত
চুপচাপ। তারপর বাচ্চাটা গলা থেকে চাকতি জাতীয় কিছু একটা খুলে নিয়ে দু’পা এগিয়ে এসে
সেটা সন্দীপের দিকে উঁচিয়ে ধরে রিনরিনে গলায় বলে উঠল,
“মেডেলটা ফেরত
দেবে না?”
আরেকটা অস্ফুট
চিৎকারের সাথেই একটা ধপ করে আওয়াজ করে দেখলাম সন্দীপের সজ্ঞাহীন দেহটা লুটিয়ে
পড়েছে মাটিতে। আর তার সাথেই আমার সামনের ওই ছেলেবেলার সন্দীপের অবয়বের আঙুলের ফাঁক
গলে চাকতির মত জিনিষটা মাটিতে ঠং করে পড়ে গেল।
এটা... এটাই কি
সেই বাইশ বছর আগের বিজ্ঞান মেধা পরীক্ষায় আমার না-পাওয়া সোনার মেডেলটা?
মুহুর্তের মধ্যে
রহস্যটা আমার চোখের সামনে উন্মোচন হয়ে গেল। আমার মনের সন্দেহটাও সত্যি বলেই পরিণত হল। প্রধান শিক্ষকের নয়নের মণি হিসাবে
পরিচিত সন্দীপের অবাধ যাতায়াত ছিল স্কুলে ওনার ঘরে। কোনও এক সময়ে ওনার
অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে হয়তো ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই মেডেলটা সরিয়ে ফেলেছিল সন্দীপ। পরে
মেডেলটা না পাওয়া যাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমাকে জানানো হয় যে মেডেলটা
আসেইনি। পরে হয়তো অনুশোচনার বশেই আমাদের এই বাড়িতে খেলাধূলার ফাঁকে ওই কুলুঙ্গীতে
মেডেলটা লুকিয়ে ফেলেছিল সন্দীপ। সরাসরি বলতে পারেনি লজ্জায়, ভয়ে। এবং এই কথাটাই
এতদিন ধরে আমাকে বলতে পারেনি ও।
মনটা অদ্ভুত একটা তিক্ততায় ভরে
গেল। একটা চাপা রাগ, ক্ষোভ আর দুঃখ মিশিয়ে গলার কাছটায় কিছু একটা দলা পাকাচ্ছে,
এমন সময়ে আর একটা জিনিষ চোখে পড়ল।
ওপরের অন্ধকার
সিঁড়ি দিয়ে এবার নেমে আসছে আরও একটা অবয়ব। একপা একপা করে সেও এবার নিচে নেমে এসে
দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে লাল একটা জামা আর হাফ প্যান্ট। চুল উস্কো-খুস্কো, দোহারা
চেহারা। পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা বাঁশির কিছুটা অংশ।
মুখ অস্পষ্ট হলেও এর পরিচয় সম্পর্কে
আমার কোনও সন্দেহ নেই। ওই লাল জামা আজ থেকে বহু বছর আগে কিনে দিয়েছিল আমার জ্যাঠা।
এতই প্রিয় ছিল যে ছোটোবেলায় সবসময় ওটাই পরে থাকতে চাইতাম। আর বাঁশির শখ ছিল বলে
দাদুর কিনে দেওয়া ওই বাঁশি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম আমি।
এরপর দেখলাম সেও
এগিয়ে এসে আগের বাচ্চাটার পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনের মুখ চাঁদের হাল্কা আলোয় এখন
আমার সামনে পরিষ্কার। বাইশ বছর আগের আমি আর সন্দীপ পাশাপাশি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।
শিরদাঁড়া দিয়ে একটা
ঠান্ডা স্রোত উঠে মাথায় পৌঁছনর আগেই বুঝলাম এবার জ্ঞান হারাব।
আর হলও তাই।
* * *
যখন জ্ঞান ফিরল
তখন সকাল হয়ে গেছে। চারিদিকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখলাম সন্দীপেরও সংজ্ঞা ফিরেছে। একটা
স্তম্ভে পিঠে হেলান দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকা কিছু একটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছে।
আমি উঠে গিয়ে
চাকতির মত জিনিষটা তুলে নিলাম।
কাল রাত্রে আমরা
কাদের দেখেছি তা জানার উপায় ছিল না। তবে যাদের দেখেছিলাম তারা অশরীরি কোনও
প্রেতাত্মা নয়। তবে তারা হল ভূত। আসলে ভূত মানেই তো অতীত। যে অতীত আমরা ফেলে এসেছি
বহু বছর আগে। ভুলে যাওয়া সময় আর ঘটনার ভীড়ে। এই ভূত বন্ধুত্বের। আমাদের দুজনেরই
অবচেতন মনের গভীরে চাপা পড়ে যাওয়া সেই বন্ধুত্বের অতীত। সন্দীপের অতীত মানতে
পারেনি তার কৃতকর্মের কথা। তাই তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল সেই জিনিষ ফিরিয়ে দেওয়ার
কথা, যার অনুশোচনার ভার এতদিন নিজের মনের গভীরে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ও। আর আমার অতীত
কেন ফিরে এসেছিল সে সম্পর্কে আমার একটা আবছা ধারণা আছে। জ্ঞান হারাবার আগে তার এগিয়ে এসে ছোটোবেলার সন্দীপের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ছোটোবেলার বন্ধুর একটা ভুলকে
ক্ষমা করে দেওয়ার কোনও ইঙ্গিত ছিল?
আমার হাতের তালুর
মধ্যে মেডেলটা সকালের সূর্যের আলোয় একবার চকমক করে উঠল। দু’ দশকের বেশি সময় হয়ে
গেলেও তার ওপরের খোদাই করা লেখাটা এখনও পড়া যায়।
“আকাশ চ্যাটার্জী”
বিজ্ঞান মেধা পরীক্ষা ১৯৯৬
প্রথম স্থানাধিকারী
।।